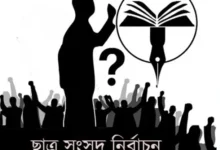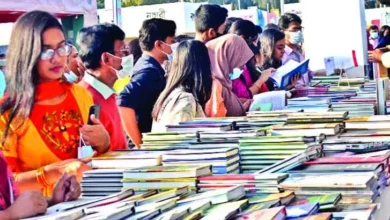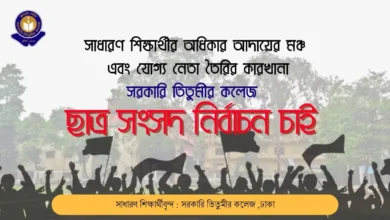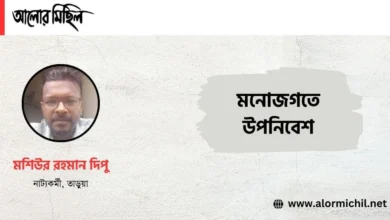আমার মতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা দেওয়া। কারণটা ঐতিহাসিক। সেজন্য কিছু পুরোনো ঘটনা বলতেই হবে।
কোম্পানিকে শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের সুবিধা সর্বপ্রথমে সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে বাংলার সুবেদার শাহজাদা শাহ সুজা দিয়েছিলেন নাকি মুঘল সম্রাট ফররুখ শিয়ার, সেটা ইতিহাসবিদরা ঠিক করুক। এখনকার প্রসঙ্গ হচ্ছে কোম্পানির শুল্কমুক্ত সুবিধা কিভাবে আমাদের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছিলো সেটার আলোচনা।
রেকর্ডেড ইতিহাসে শুল্কমুক্তি সুবিধা নিয়ে কোম্পানির প্রথম বিরোধ দেখতে পাই সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খানের আমলে। তারপর সেই শায়েস্তা খানের আমল থেকে বাংলার সর্বশেষ নবাব মীর কাসিমের আমল পর্যন্ত কোম্পানির শুল্কমুক্ত সুবিধা নিয়ে বিরোধের বিষয় একটাই ছিল। সেটা হচ্ছে, কোম্পানিকে প্রতিষ্ঠান হিসেবে যে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়া হয়েছে সেটার সুবিধা কি কোম্পানির কর্মচারীরাও পাবেন কিনা। কারণ কোম্পানির পণ্য নিয়ে কোম্পানির কর্মচারীরাও ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যবসা করতেন।
শাহজাদা শাহ সুজা কোম্পানিকে যেই শুল্কমুক্ত সুবিধা দিয়েছিলেন, সেটা কোম্পানির কর্মচারীরা অপব্যবহার করায় যে প্রথম বিরোধ সৃষ্টি হয় তাতে শায়েস্তা খানের সাথে কোম্পানির যুদ্ধ হয়েছিলো এবং কোম্পানি তাতে পরাজিত হয়েছিলো। কিন্তু এরপর ১৭৫৭ এর পলাশী বিজয়ের আগেও কোম্পানির কর্মচারীরা বিভিন্ন কৌশলে বিপুল পরিমাণে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে কোম্পানির পণ্য নিয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন।
১৭৫৭ এর পর একটা সময়ে মীর কাসিম যখন নবাব হোন তখন কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা পরিচালনায় ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার বিষয় নিয়েই কোম্পানির সাথে বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং তারই জেরে অবশেষে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হোন।
মীর কাশিমের পর এই দুর্নীতি এমন লাগামছাড়া পর্যায়ে চলে যায় যে, খোদ কোম্পানির প্রশাসকরাও এর বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেননি। ট্যাক্স ফাঁকি দেবার কারণে কোম্পানির কর্মচারীরা কোম্পানির পণ্য একদম কম দামে বিক্রি করতে পারতো, আর অপরদিকে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের উপর তুলনামূলক অনেক উচ্চহারে কর আরোপ করা হতো। এই অসম প্রতিযোগীতায় খুব দ্রুতই বাংলার স্থানীয় ব্যবসায়ী আর সমৃদ্ধ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিপর্যয়ের মুখে পড়ে।
সেই সময়েই মসলিন শিল্পীদের “আঙুল কেটে” ফেলার বিষয়টা প্রচলিত হয়। আক্ষরিক অর্থেই মসলিন শিল্পীদের আঙুল কাঁটা হয়েছিলো কিনা সেটা নিয়ে বিতর্ক আছে, কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীদের ট্যাক্স ফাঁকির দুর্নীতির সুবাদে মসলিন শিল্পীদের কারখানা একের পর এক বন্ধ হয়ে যায়। ফলে প্রায়োগিক অর্থে তাদের আঙুল মসলিন তৈরির আর কোন কাজে আসেনি।
কোম্পানির কর্মচারীদের ট্যাক্স ফাঁকির ফলে স্থানীয় ব্যবসায়ী আর ক্ষুদ্র-কুটির শিল্পীরা কর্মহীন হয়ে পড়ে আর বাংলার রাজস্ব ভাণ্ডার হয়ে পড়ে শূণ্য। এর অবধারিত ফলাফল হিসেবে আমাদের সামনে আসে ইংরেজি সন ১৭৭০ অথবা বাংলা সন ১১৭৬ এর দুর্ভিক্ষ। যাকে আমরা বলি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। অর্থাৎ ১৭৫৭ এর সময়েও বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ অঞ্চল বাংলা, মাত্র ১৩ বছরের মাথায় কোম্পানির কর্মচারীদের ট্যাক্স ফাঁকিতে নিঃস্ব হয়ে যায়। একদিকে মোট তিন কোটি জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় এক কোটি দুর্ভিক্ষে মারা যায় আর আরেকদিকে কোম্পানির কর্মচারি যাদের মধ্যে ব্রিটিশ ও স্থানীয় উভয়েই বিদ্যমান, তারা বিপুল পরিমাণ অর্থের মালিক হয়ে যান।
সেই সময়ের কোম্পানি কর্মচারীদের ক্ষমতার একটা উদাহরণ দেই। ১৭৫৭ এর পলাশী যুদ্ধের সময়কালে রবার্ট ক্লাইভের অধীনে ওয়ারেন হেস্টিংস চাকরি করতেন। ১৭৫৭ এর পর তিনি এই দুর্নীতির ব্যাপারে সোচ্চার হয়ে চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারপর তিনি ইংল্যান্ডে চলে যান। পরে ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতে ব্রিটেনের প্রথম এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের পদ গভর্নর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে ইংল্যান্ড থেকে ফেরত এসেছিলেন। কিন্তু তারপরও তিনি কোম্পানির কর্মচারীদের ট্যাক্স ফাঁকির দুর্নীতি বন্ধ করতে পারেননি।
এই অতি ধনী কোম্পানির কর্মচারীরাই পরবর্তীতে কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার সুযোগে জমিদারি কেনা শুরু করেন। তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের অবশ্য পাঠ্য তিন খন্ডের উপন্যাস “কীর্তিহাটের কড়চা” তে এমন একটা জমিদার পরিবারের গল্প আছে। এই উপন্যাসে ১৭৯০ সালের পর থেকে ভারতের স্বাধীনতা পরবর্তী প্রজাতন্ত্রী সময়ের সমাজ আর ইতিহাসের রুপান্তরের নিখুঁত বর্ণনা আছে। কারণ তারাশংকর নিজেও এমন একটি জমিদার পরিবারে বংশধরে ছিলেন।
ব্রিটিশ সরকারে সুবিধাভোগী বাংলার এই জমিদার শ্রেণী ভারতে ব্রিটিশরাজ টিকে থাকার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলো। এমনকি ভারতের ১৮৫৭’র সিপাহী বিদ্রোহ, যাকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে উল্লেখ করা হয়, সেই সময়ে বাংলার জমিদার, ব্যবসায়ী ও শিক্ষিত পেশাজীবিরা (আইনজীবি, ডাক্তার, অফিসের বাবু প্রমুখ) ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে ছিলেন।
যেই ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা আর শিক্ষা আমাদেরকে পরাধীনতার সুবিধাভোগ করতে শেখালো। আবার সেই ব্রিটিশ শাসন আর তার শিক্ষাই লর্ড ম্যাকুইলের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী আমাদের ভেতরে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তৈরি করলো। কিভাবে এই রুপান্তরটা হলো সেটা জানার জন্য অবশ্য, অবশ্য এবং অবশ্য পাঠ্য হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনের অধীন লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সে প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের ডক্টরেটকালীন সময়ে জমা না দেওয়া পিএইচডি ডিসার্টেশন “Political Parties in India”, এটি বই আকারে ইউপিএল থেকে প্রকাশ করা হয়েছে।
আপনাদের আর এসব পুরোনো কথা বলে পাকাবো না। সরাসরি এখন ১৯৪৭ থেকে ২০২৪ এ চলে আসি। ৫ আগস্টের বিপ্লবের আগ মূহুর্তে সুদীর্ঘ ১৬ বছরের যে স্বৈরাচার ছিল, তার একটা নিদারুণ বৈশিষ্ট্য ছিল কালো টাকা সাদা করার বিধান। এই মূল কথা হলো, আপনার অবৈধ বা অপ্রকাশিত আয়কে নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় বিনিয়োগ করলে এনবিআর আর জানতে চাইবে না যে আপনি এই টাকা কিভাবে আয় করেছেন।
সাধারণত অবৈধ আয় বিষয়টি মূলত সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য, আর অপ্রকাশিত আয়ের বিষয়টি মূলত ব্যবসায়ীদের জন্য প্রযোজ্য। এই অবৈধ আয় সরকারি কর্মচারীরা কিভাবে করেন আর ব্যবসায়ীরা কিভাবে তাদের আয় অপ্রকাশিত রাখেন সেটার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু একটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর তা হলো, সরকারি কর্মচারী আর ব্যবসায়ীরা এই লুটপাটের ক্ষেত্রে একে অপরের সহায়ক। কিভাবে? সরকারি কর্মচারী অবৈধ আয় দিয়ে মূলত যে ফ্ল্যাট-প্লট ক্রয় করেন আর বিদেশে অর্থ পাচার করেন, তাকে এই কাজে সহায়তা করে ব্যবসায়ীরা। আর ব্যবসায়ীরা তাদের আয়কে অপ্রকাশিত রাখার জন্য সরকারি কর্মচারীদের সহায়তায় সম্পত্তির মূল্য কম করে দেখান, ভ্যাট ফাঁকি দেন, বিদেশে ভুয়া নামে নিজেদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কাছেই আমদানির নামে টাকা পাচার করেন।
আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলের দুর্নীতিবাজ কর্মচারীরাই ছিল ব্যবসায়ী। আর ২০০-২৫০ বছর পর এই শ্রেণীটাই সরকারি কর্মচারী আর ব্যবসায়ী এই দুইভাগে ভাগ হয়েও বলতে গেলে দুই দেহ এক আত্মা হয়ে আগের মতোনই এক হয়ে দেশ আর দেশের মানুষকে লুট করে যাচ্ছে।
এই কালো টাকা সাদা করার বিধান সর্বপ্রথম বাংলাদেশে করা হয় ১৯৭৫ সালের ৭ ডিসেম্বর । তারপর থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন নামের, বিভিন্ন আদর্শের, বিভিন্ন দলের সরকার এই দেশে ক্ষমতায় এসেছে। অনেক বিষয়ে তাদের ভিন্ন মত থাকলেও, কালো টাকা সাদা করার ব্যাপারে তাদের পলিসি অভিন্ন ছিল। না হয়েও উপায় ছিল না। কারণ ১৭৫৭ তে ব্রিটিশদের কাছে বাংলার পতনের পর যেই ব্যবস্থায় সরকার পরিচালিত হয় তা মূলত সরকারি কর্মচারি আর ব্যবসায়ী প্রভাবিত শাসনব্যবস্থা। একে আপনি “কলোনিয়াল”, “ঔপনিবেশ”, “ব্রিটিশ” যে নামেই ডাকুন না কেন, জিনিস ওই একই। আমি একে ডাকি “পরাধীন শাসনব্যবস্থা” নামে। কারণ এই শাসনব্যবস্থায় আমরা সবসময় সরাসরি বা ঘুরিয়ে পেচিয়ে পরাধীন থেকেছি।
১৯৭১ এর ২৫ মার্চের পর আবার ২০২৪ এর ৫ আগস্টের পর আমরা নিজেদের স্বাধীন বলছি ঠিকই, কিন্তু এখনও আমাদের ভালো থাকা বা মন্দ থাকা কোন না কোন বিদেশি শক্তির অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। এর আগে ছিল ভারত, রাশিয়া, চায়না। এখন হয়েছে আমেরিকা, ব্রিটেন আর পশ্চিম ইউরোপ। এক সময়ের সমৃদ্ধশালী মসলিন আর জামদানির বাংলাকে এখন ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় যে এই বুঝি আমেরিকা আর পশ্চিম ইউরোপ আমাদের গার্মেন্টসের অর্ডার বাতিল করে দিবে!
এখনকার অন্তবর্তীকালীন সরকার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং তারিখের “এসআরও নং ৩০৩-আইন/আয়কর-৪৬/২০২৪।“ এর মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করার বিধান বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও আমরা আশাবাদী হতে পারছি না। কারণ পরাধীন শাসনব্যবস্থায় আমাদের দেশে এই বিধান আগেও সাময়িকভাবে বাতিল হয়ে আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
আমরা ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে দেখেছি যে, পরাধীন শাসনব্যবস্থায় সরকারি কর্মচারী আর ব্যবসায়ীদের দুর্নীতিতে কিভাবে আমরা স্বাধীনতা হারিয়েছি আর কিভাবে দুর্ভিক্ষে আর দারিদ্র্যে আমাদের পূর্বপুরুষদের মরে যেতে হয়েছে।
আমরা দেখেছি যে, পরাধীন শাসনব্যবস্থা না বদলানোর কারণে ১৯৭১ সালে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে ও লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকেও লুট করে সরকারি কর্মচারি আর ব্যবসায়ী শ্রেণী কিভাবে সম্পদের পাহাড় গড়েছেন। এই পরাধীন শাসনব্যবস্থা সংস্কার না করে শুধু একটি-দুইটি বিধান বাতিল বা যোগ করলে ২০২৪ সালেও সেই ১৭৫৭ আবার ফিরে আসবে।
আমরা কোরবানির ঈদে কোন এক গরু বা ছাগলের দামের সূত্র ধরে সেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীর কোন এক বর্তমান আদর্শিক বংশধরকে বারবার খুঁজে পাবো।
আপনার, আমার, আমাদের রাজনৈতিক আদর্শে ভিন্নতা থাকতেই পারে, থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাধীনতার প্রশ্নে আমাদের সবার অবস্থান এক ও অভিন্ন। পরাধীন শাসনব্যবস্থা বাতিল না করা পর্যন্ত আমরা কেউই স্বাধীন না।